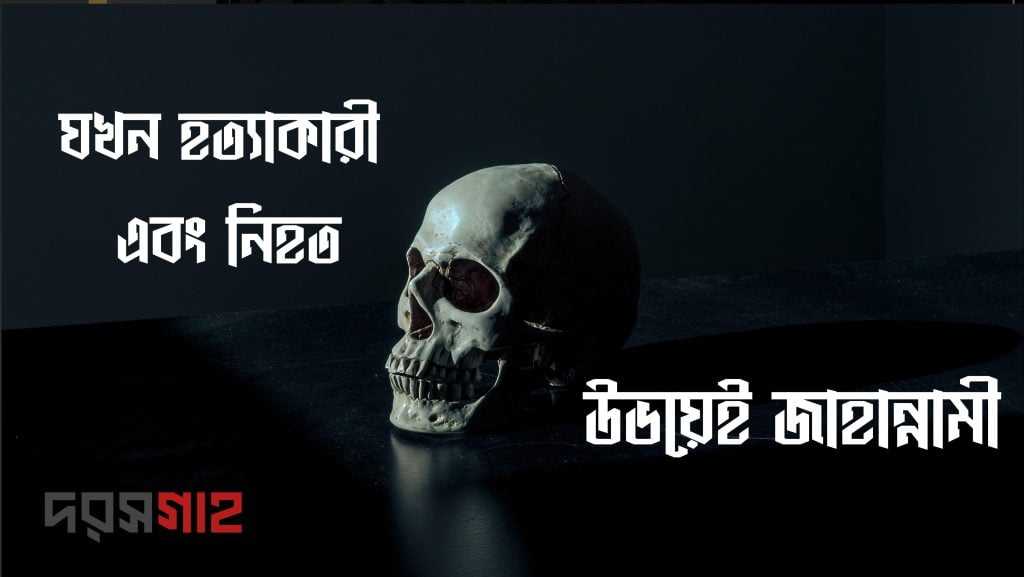ড. জাভেদ আকবর আনসারীর লেখা অবলম্বনে
পুঁজিবাদ; একটি জীবনব্যবস্থাঃ ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি
আব্দুল্লাহ বিন বশির হাফি.
১.১ পুঁজিবাদের ইতিহাস
এনালাইনটেনমেন্ট আন্দোলনের ভিত রচনাকারী চিন্তাবিদগণ মনে করেন, পুঁজিবাদের বিজয় হিউম্যান বিয়িংয়ের পরিপক্কতার বহিঃপ্রকাশ। কান্টের বক্তব্য মতে, ‘মানুষ যখন অপরিপক্ক ছিলো, নিজের সবকিছুতেই সে স্রষ্টার মুখাপেক্ষী ছিলো। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতিতে মানুষ পরিপক্কতায় পৌঁছে। এবং মানুষের অনুভূত হয়ে যায়, সে নিজেই নিজের স্রষ্টা, স্বনির্ভর, স্বায়ত্ত্বশাসিত এবং সকল কিছু থেকে অমু্খাপেক্ষী।’
ইতিহাসের পরিক্রমায় এটা প্রমাণিত হয়েছে, ইউরোপে ‘মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা অর্থাৎ সে হিউম্যান বিয়িং’ এই ধারণা ধ্বংস করে দিয়েছে খ্রিস্টান জীবনব্যবস্থাকে।
খ্রিষ্টবাদ ইউরোপে তিনশত বছরের কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খ্রিষ্ট শতাব্দীতে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক ও ধর্মের প্রধানরা ইউরোপে অপরিচিত ও অত্যাচারিত ছিলো। তখন ইউরোপীয় সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে বিভিন্ন বস্তুপূজা এবং যাদুকরদের উপাসনা ছিলো ব্যাপক। ব্যক্তি থেকে সামাজিক জীবন— সবখানেই অনৈতিকতা ছিলো বিরাজমান।
ইউরোপের এই অধঃপতিত সমাজের জন্য খ্রিস্টানরা এক আলোকবর্তিতা হয়ে দেখা দিলো। আধ্যাত্মিকতা ও উত্তম চরিত্র মানুষের মাঝে পেশ করে সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে লাগলো। সমাজের এই সংস্করণে আর খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও উন্নতির জন্য তারা যে কুরবানী আর ত্যাগ দিলো তা ছিলো বে-হিসাব। আর এর ফলেই ইউরোপীয় সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়। খ্রিস্টানদের নেতৃত্ব অর্জন হয়ে গেলো। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা খ্রিষ্টধর্মে দিক্ষিত হতে লাগলো এবং খ্রিস্টানধর্মের প্রধানদেরকেই নিজেদের পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিলো।
কিন্তু এতসব ত্যাগ আর কুরবানীর পরেও খ্রিস্টান ধর্মের প্রধান সেন্ট পিটারের মৃত্যুর পর খ্রিস্টানদের এক শ্রেণি ইউরোপের বিভিন্ন কুফরি ব্যবস্থার সাথে সন্ধি স্থাপনের পথ গ্রহণ করে নেয়। এই সমঝোতার তিনটি দিক ছিলো। যার মাঝে সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি ছিলো, ইসা আ.-এর রেখে যাওয়া শিক্ষাকে বিকৃত করে ইউরোপের বিভিন্ন কুফরি বিশ্বাসগুলোকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া। আর একাজের অন্যতম আঞ্জামদাতা ছিলো সেন্ট পল। সে মুসা আ.-এর ঐ সমস্ত শিক্ষাকে ধীরে ধীরে বাতিল করে দিলো যেগুলো প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো ইসা আ.-এর নবুওয়াতের অন্যতম কাজ। প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিষ্টশতাব্দীতে ত্রিত্ত্ববাদ (Doctrine Of Trinity) সম্পর্কে যেখানে খ্রিস্টানদের কোনো ধারণাই ছিলো না, সেখানে আকলবহির্ভূত ও শিরকি এই আকিদাকে পরবর্তীতে ধর্মের মৌলিক আকিদা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলা হলো। অন্যদিকে বিভিন্ন ভ্রান্ত রুসম যেমন ক্রিসমাস, ইস্টার, সেন্ট ডেইজ— এগুলোকে খ্রিষ্ট ধর্মের মাঝে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এবং বিভিন্ন মূর্তি ও গাছকে গির্জায় প্রবেশ করিয়ে তার পূজা-অর্চনা হতে লাগলো। এভাবে বাইতুল মাকদিসের খ্রিস্টানদের সাথে ইউরোপের খ্রিস্টানদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলো আর ইউরোপিয়ান খ্রিস্টানরা রোমান সম্রাজ্যের সাথে মিলিত থেকে আলাদা হয়ে গেলো।
চতুর্থ খ্রিষ্টশতাব্দীতে যখন রোমান শাসক কন্সটান্টাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে তখন খ্রিষ্ট শাসনব্যবস্থা ও রোমান শাসনব্যবস্থা একীভূত হয়ে গেলো। যার আবশ্যকীয় ফল ছিলো, খ্রিস্টান ধর্মের আধ্যাত্মিকতা ও চারিত্রিক শিক্ষার প্রভাব ব্যাপকভাবে কমে যেতে থাকলো এবং আধ্যাত্মিকতা ও উত্তম চরিত্রের যে ধর্মীয় মানদণ্ড ছিলো তা সমাজে আর বাকি থাকলো না। তখন পাদ্রীরা রোমান রাজপরিবারের সাথে মিলে পলের তৈরিকৃত বিকৃত খ্রিষ্টধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে রোমান শাসনক্ষমতা ব্যবহার করতে লাগলো।
এভাবে প্রায় এক হাজার বছর (চতুর্থ খ্রিষ্টশতাব্দী থেকে চতুর্দশ খ্রিষ্টশতাব্দী পর্যন্ত) ইউরোপীয় সমাজে খ্রিস্টানধর্ম বিজয়ী ছিলো। রোমান ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় খ্রিষ্টীয় শাসনবব্যবস্থা মজবুত হতে থাকলো। কিন্তু এই পুরো সময়টাতে খ্রিষ্টধর্মের আধ্যাত্মিকতা ও চারিত্রিক শিক্ষা একদম শেষ হয়ে গেলো। জনসাধারণের মধ্যে এমনকি গির্জার মাঝে বদ চরিত্র ও অনৈতিকতা একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গেলো। ঠিক ঐ সময়ে খ্রিষ্টধর্মের সাথে পরিচয় হয় ইসলাম ধর্মের। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা সর্বদা ইসলামকে তাদের প্রধান শত্রু গণ্য করেছে এবং ইউরোপ থেকে ইসলামকে বের করে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় ফ্রেডরিক (Fredrick II), চার্লিম্যান (Charlemagne) এর মত জালেম ও রক্তচোষা শাসকদের সঙ্গ দিয়েছে।
কিছু খ্রিস্টান পাদ্রী ছিলো তার ব্যতিক্রম। তারা এই প্রয়োজনীতা অনুভব করছিলো যে, ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে ব্যাপক হোক। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো সেন্ট ফ্রান্সিস। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সে ইউরোপের সামনে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান পেশ করে। এবং ক্রুসেড যুদ্ধ শেষ করারও যথেষ্ট চেষ্টা করে। এমনকি সেন্ট ফ্রান্সিস ইউরোপে ইসলামের মত করে একটি সুফি সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো।
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ স্পেন ও ফ্রান্সে ক্যাথারদের একটি শক্তিশালী আন্দোলন শুরু হয়, যাকে ক্যাথার আন্দোলন (cathar) বলা হয়। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট (Pope Innocent) ফ্রান্সের রাজার সাথে মিলিত হয়ে আরেকটি ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা করে। এবং আন্দোলনকে শক্তভাবে দমন করে ফেলে।
অষ্টম থেকে পনেরো খ্রিষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত স্পেনে মুসলিমদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু স্পেনের মুসলিম সমাজে সর্বদা মুতাজিলা ও কাদরিয়া ফিরকার প্রভাব বেশি ছিলো। আর সে ফিরকা দুটোর জ্ঞানচর্চার নীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ইউরোপ থেকে আসা খ্রিস্টান ছাত্রদের। আর এই জ্ঞানচর্চার কারণেই ইউরোপের খ্রিস্টানদের মাঝে প্লেটো (Neo Platonism) এবং অ্যারিস্টিটলের (Aristotle) দর্শনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
মুসলিম বিশ্বে তখন প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শন ও সেগুলোর প্রচারকদের ইমাম শা’রানী, গাজালি ও ইবনে তাইমিয়া রহ. প্রমুখগণ নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন এবং এদের বিদ্যার অসারতা থেকে ইসলামি জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতাকে পূর্ণরূপে হেফাজত করেছেন। আর এই কারণে মুসলিম বিশ্বে পুঁজিবাদি জ্ঞানতত্ত্ব ও জীবনব্যবস্থা ইউরোপীয় সভ্যতার বিজয় ও সাম্রাজ্যবাদের পূর্বে প্রবেশ করতে পারেনি। এটা নিয়ে মুসলিম মর্ডানিস্টদের আফসোসের কোনো শেষ নেই। কবি ইকবাল (reconstruction of Religious Thougt in Islam) থেকে নিয়ে আমির আলি (A History of the Saracens) ড. ফজলুর রহমান (Islam) সকলেই ইসলামের পশ্চাৎপদতার জন্য ইমাম গাজালিকে একধরণের দায়ি করে। পশ্চাৎপদতার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসলিম বিশ্বে পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থা উন্নতি লাভ করতে না পারা। দরকার ছিলো পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থাকে ইউরোপের পূর্বে মুসলিম বিশ্বে গ্রহণ করে নেওয়া। কেননা মুতাজিলারা ইউরোপের পূর্বেই গ্রিক দর্শনবিদ্যা পূর্ণ আয়ত্ব করে নিয়েছিলো। এবং তাদের মাধ্যমে ইউরোপে তা পৌঁছে। বিপরীতে ইউরোপে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শন খ্রিস্টানদের জ্ঞানতত্ত্বে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এগারো শতকেরও অনেক পরে।
ইউরোপে দর্শনচর্চা এতটাই বাড়তে থাকে যে, একসময় ধর্মের বিষয়গুলোকেও দর্শনবিদ্যা দিয়ে প্রমাণ করার একটা মানসিকতা তৈরি হয়। আর দর্শনচর্চা যে জ্ঞানতত্ত্বের পথ ধরে খ্রিস্টধর্মে প্রবেশ করে তাকে বলা হয় স্কলাসটিজম (Scholasticsm) বা ধর্মীয় দর্শন(১)। স্কলাসটিজমের অন্যতম চিন্তাবিদ ছিলো টমাস একুইনাস। যে নিজেকে স্পেনের মুসলিম মহান মনীষী ইবনে রুশদের ছাত্র পরিচয় দিয়ে গর্ব করতো।
প্রাচীন গ্রীসের দর্শনচর্চার ফল খ্রিষ্টবিশ্বে এই দাঁড়ালো যে, ধর্মের আকিদা-বিশ্বাসগুলোর বৈধতা আর নির্ভরযোগ্যতা বাইবেল আর ধর্মীয় টেক্সটের বদলে এখন অ্যারিস্টটিলীয় যুক্তির আলোকে সাজানো শুরু হলো। আর এভাবে একপর্যায়ে যুক্তি ও আকলকে ধর্মের আকিদা-বিশ্বাসের মানদণ্ড হিসেবে ব্যাপকভাবে মানুষ মেনে নিতে লাগলো। অন্যদিকে সময়ের অতিক্রান্তে এই যুক্তি ও আকলের মাধ্যমেই একদল মানুষ খ্রিষ্টধর্মকে ভুল প্রমাণ শুরু করতে লাগলো। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন আকিদা-বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে কিছু পাদ্রীরাই প্রশ্নবিদ্ধ করে বসে। বিশেষত ত্রিত্ববাদ ছিলো সমালোচনার সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তু। স্কলাসটিজমের মাধ্যমে ত্রিত্ববাদের আকিদার বিপরীত অবস্থান নেওয়া বিদ্রোহীদের থেকে আরো একধাপ আগে বেড়ে বিজ্ঞান এসে প্লোটো আর অ্যারিস্টটলের দর্শনকেই ‘ভুল’ বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো। যেহুতু খ্রিস্টান ধর্মের আকিদা-বিশ্বাসগুলো এই পর্যায়ে এসে প্লোটো আর অ্যারিস্টটলের দার্শনিক বিদ্যার মাধ্যমে বৈধতার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছিলো, এখন সেগুলোর ভুল প্রমাণ হওয়া এক অর্থে খ্রিস্টানধর্ম ভুল হওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ালো। ষোড়শ, বিশেষত সপ্তদশ শতকে কতক প্রভাবশালী বিজ্ঞানীদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো কোপার নিকাস, নিউটন ও গ্যালিলিও। এই মতবাদ খ্রিষ্টধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্বভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। বিজ্ঞানের বিজয় এই অর্থে খ্রিষ্টধর্মের পরাজয় যে, বিজ্ঞান খ্রিষ্টীয় স্কলাটিজিষ্টদের দাবি ‘অ্যারিস্টটলের দর্শন ধর্মের মতই অকাট্য’—এটাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করে দেয়। বিজ্ঞান এটা প্রমাণ করে যে, মানুষ এই বিষয়ে সক্ষম যে, নিজের পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশক্তির মাধ্যমে মহাবিশ্বের বস্তুগত গঠন ও গতি বুঝে সেগুলোকে আয়ত্ব করে নিজেদের অনুগামী করে ফেলতে সক্ষম। আর এই জন্য মানুষের কোনো আসমানী ওহি বা বার্তার প্রয়োজন নেই। বরং আসমানী ওহি (খ্রিস্টান ধর্মের দর্শন ব্যাখ্যা) পৃথিবীর ঘনত্ব ও গতি সম্পর্কে যে তথ্য দেয় তা সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত।
সপ্তদশ শতাব্দীতে নিত্যনতুন আবিষ্কার ও জ্ঞানের উদ্ভাবন অষ্টাদশ শতাব্দীতে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের সফলতার রাস্তা প্রশস্ত করে দেয়। আন্দোলনের মৌলিক দাবি এটাই ছিলো যে, মানুষ জীবনের কোনো বিষয়েই ওহির মুখাপেক্ষী না। সে একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী এক সত্তা। সে যেমন নিজেই নিজের স্রষ্টা তদ্রুপ সে এই বিশ্বেরও স্রষ্টা। এনালাইটেনমেন্ট আন্দোলন থেকে সৃষ্ট এই ধারণাগুলোকে হিউম্যানিজম বলা হয়। এগুলোকে এতটাই অকাট্ট জ্ঞান ধারণা করা হয়, যেমন ধর্মের মাঝে স্রষ্টার ধারণাকে মনে করা হয়। কোনো অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ বা গবেষণা এই কথার প্রমাণ করেনা যে, মানুষ হলো ‘হিউম্যানবিয়িং’—স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বায়ত্ত্বশাসিত, সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী এক সত্তা এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। বিজ্ঞান খ্রিষ্টধর্মের জ্ঞানতত্ত্বের পদ্ধতি স্কলাসটিজমকে সম্পূর্ণ আকল বহির্ভূত প্রমাণ করে দেয়। এবং এমন সব থিউরি সামনে আনে যার মাধ্যমে মানুষ হিউম্যান বিয়িং বা ব্যক্তিমানবে পরিণত হয় এবং নিজ সত্তার প্রভুত্বের উপর ঈমান স্থাপন করে। মহা বিশ্বের সকল বস্তুগত শক্তিকে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়ে যায়।
বিজ্ঞান মানুষকে হিউম্যান বিয়িং বা ব্যক্তিমানব বানিয়ে দেয়না। তবে বিজ্ঞান শুধু সে সমাজেই নিজেকে পূর্ণ মেলে ধরতে পারে, যেখানে অধিকাংশ মানুষ নিজেকে হিউম্যান বিয়িং মনে করে এবং দুনিয়াকে বশীভূত করে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে। এই অর্থে বিজ্ঞান হলো পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থার প্রাকৃতিক জ্ঞান।
১.২ পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থার কার্যত ভিত্তি
ইউরোপে পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মৌলিক কারণ খ্রিষ্টধর্মের জ্ঞানতত্ত্বের পরাজয় নয় বরং নৈতিকচরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার অধঃপতন। যা একাদশ ও দ্বাদশ শতকে সংগঠিত হওয়া ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিস্টান সৈন্যদের হত্যা আর লুটপাটের মাধ্যমে পূর্ণ প্রকাশিত হয়। সম্পদ লুটপাট আর বর্বরতার এই ভয়ংকর চিত্র আরো বড় আকারে প্রকাশ পায় চথুর্দশ ও পঞ্চাদশ শতকে স্পেনের মুসলিম নিধনে। এভাবে হত্যা আর লুটপাট করে সম্পদ অর্জনের মজা পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইউরোপের বড় বড় প্রতিটি রাজ্য ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল—সকলে হামলে পড়ে পূর্ব ও দক্ষিণ আমেরিকায়। সেখানে তারা ধারণাতীত লুটপাট, হত্যা আর ধর্ষণ চালিয়ে চার শতাব্দী ধরে ৮ কোটি রেড ইন্ডিয়ানদের হত্যা করে। চোখের পলকেই উন্নত সভ্য একটি জাতীকে জাতিগত নিধনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয় সভ্যতার ধ্বজাধারী আধুনিক এই ইউরোপীয়ানরা। অষ্টাদশ শতকের শুরুতে বর্বরতার এই ইউরোপীয় সয়লাব এসে হানা দেয় আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও পর্তুগালের নতুন উপনিবেশ তৈরি হয় সে অঞ্চলগুলোতে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো সাম্রাজ্যবাদের এই সময়ে ৮০ কোটি মানুষকে হত্যা করে দুনিয়ার সকল সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়।
ষোড়শ শতাব্দীর পর ইউরোপে স্বর্ণ-রূপা, হীরা-চাঁদি, বিভিন্ন খনিজ সম্পদ জমা হতে থাকে। ধারাবাহিক এই লুটপাটের সম্পদের মাধ্যমে ইউরোপের দেশগুলোতে সম্পদের যে স্তুপ জমা হয় তাতে প্রতিটি ইউরোপীয়ান ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে। আর এমন অবস্থায় নৈতিকতার শিক্ষাহীন যেকোনো জাতির মাঝে হিংসা, লোভ, স্বার্থপরতা—এককথায় পশুর স্বভাবে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ছিলো। বৈশ্বিক এই হত্যা, ধোঁকাবাজি আর লুটপাট ইউরোপে যে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করেছে তার ফলাফল হলো, প্রতিটি ইউরোপীয়ান নাগরিক পুঁজিবাদি শাসন, পুঁজিবাদি চরিত্র ও পুঁজিবাদি আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে ঐ মানুষগুলোই বেশি সম্মানিত ও প্রভাবশালী হতে থাকলো, যে সবচেয়ে বেশি লোভি, হিংসুক, স্বার্থপর ও খোদাদ্রোহী।
ক্রুসেড যুদ্ধের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার হত্যা, ধোঁকাবাজী ও লুন্ঠন ধারাবাহিক চলে আসছে। এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে চলা এই হত্যাযজ্ঞের পুরো সময় প্রতিটি স্তরে সাম্রাজ্যবাদিদের একান্ত সহযোগী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে খ্রিষ্টধর্মগুরুরা। উত্তর আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানদের জাতিগত নিধনের শুরু যে করেছে এবং সে হত্যার বৈধতার পক্ষে ওকালতি করেছে, সে খ্রিস্টধর্মের একজন পবিত্র ধর্মগুরু। যাকে আজও আমেরিকার মানুষরা সম্মানের সাথে Pilgrim fathers-এর মতো পবত্রি নামে স্মরণ করে। রোমের প্রধান পাদ্রী দক্ষিণ আমেরিকাকে স্পেনের এবং পর্তুগালের মাঝে ভাগ করে দেয়। ইন্দোনেশিয়ার উপর হল্যাণ্ডের আক্রমণও এই ধর্মগুরুদের উসকানিতেই হয়েছে। ফিলিপাইন, আফ্রিকা, ফিজি ও আলজেরিয়ায় খ্রিস্টান পাদ্রীরা সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের হিম্মত ও উৎসাহ প্রধানের কাজ ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করেই আঞ্জাম দিয়েছে। আজকের সময়েও আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে খ্রিষ্টান মিশনারীগুলো।
খ্রিষ্টধর্মগুরুদের উপনেবেশবাদের সাথে মুনাফিকি অংশগ্রহণের এহেন চিত্র খ্রিষ্ট বিশ্বের মানুষের কাছেও খ্রিস্টান ধর্ম প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয়। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, খ্রিষ্টসমাজে ধর্মকে গুরুত্বহীন ও অবিবেচনার বস্তু হিসেবে ধারণা করতে লাগলো। মানুষ ধীরে ধীরে খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা শুরু করলো। খ্রিষ্টধর্মকে যখন বিজ্ঞান আর এনালাইটেনমেন্ট আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হলো, তখন ইউরোপের বেশির অংশ খ্রিষ্টধর্মের আদর্শকে যুক্তি-বিচার ও আকল বহির্ভূত দারির প্রবক্তা হয়ে গেলো। অবস্থা এই দাঁড়ালো, অধিকাংশ মানুষ হয় খ্রিস্টান ধর্মকে পূর্ব অভ্যাসের কারণে গ্রহণ করে রেখেছে বা শাসন ব্যবস্থার চাপে ত্যাগ করার সাহস করছে না।
১.৩ পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন
পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থাকে পূর্ণরূপে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করা হয় ত্রয়োদশ খ্রিষ্ট শতাব্দীতে ইটালীর কিছু শহরে। এই শহরগুলো পাদ্রী ও ইউরোপের শাসনব্যবস্থা থেকে অনেকটা স্বাধীন ছিলো। তার মাঝে প্রসিদ্ধ কিছু শহর ছিলো ফ্লোরেন্স, মিলান, নেপোলী ও ভিন্স।
পোপতন্ত্র যেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলো তার নামকরণ করা হয় ‘হোলি রোমান এম্পায়ার’, যা শারলেমিনের বিজয়ের পর অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুমানিক ৭০০ বছর তা কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ‘হোলি রোমান এম্পায়ার’ বা পোপতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মান শাসকরা যুদ্ধের মাধ্যমে একদম দুর্বল প্রভাবহীন করে দেয়।
পোপতন্ত্র মুক্ত পুঁজিপতিশ্রেণির রাজনৈতিক বিজয়কে বুর্জোয়াশ্রেণীর (bourgeoisie) বিজয় বলা হতে থাকে। এই পুঁজিপতি শ্রেণি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মাঝে সুদভিত্তিক লেনদেন, ব্যবসা ও কারবার শুরু করে। যাদের মাঝে অগ্রগণ্য ছিলো ইহুদিরা। এরাই প্রথম ব্যাংকসিস্টেম ও ফাইন্যান্স আবিষ্কার করে। আর এভাবেই এই শহরগুলোতে ইতিহাসে প্রথম পুঁজিবাদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। পঞ্চাদশ শতকে ইটালির এই শহরগুলোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইউরোপের ধনী ব্যবসায়ী, মহাজন ও জুয়ারীরা হয়ে গেলো। এরা পুরো ইউরোপে সুদি কারবার, জুয়া এবং পুঁজিবাদি অর্থের জাল বিছিয়ে দেয়।
এভাবেই এনালাইটেনমেন্ট আন্দোলন প্রতিষ্ঠত হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই পুরো ইউরোপে পুঁজিবাদি শাসনব্যবস্থা বিজয়ী হয়ে যায়।
পুঁজিবাদ সর্বপ্রথম কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একাডেমিকভাবে এর ভিন্ন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। এলেন উড (Ellen wood) এবং রবার্ট ব্রেনার (Robert Brenner)-এর বক্তব্য হলো— সর্বপ্রথম পুঁজিবাদ ব্যাপক হয় ইংল্যান্ডে পনেরশ শতাব্দীতে। আবার অন্যান্য কিছু গবেষণা অনুযায়ী পুঁজিবাদি শাসনব্যবস্থা সর্বপ্রথম গৃহীত হয় ফ্রান্সের মার্সেই (marseilles) শহরে।
১.৪ পুঁজিবাদের কবলে ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ
ত্রয়োদশ শতক থেকে রোমান পাদ্রীদের সাথে ‘হোলি রোমান এম্পায়ারের’ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। ঐ দ্বন্দ্বের সময়ে পোপ আঞ্চলিক রাজাদের হোলি রোমান এম্পায়ারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের রাজাদের সাহায্যে হোলি রোমান এম্পায়ারকে পরাজিত করে। কিন্তু পরবর্তীতে নিজ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে প্রত্যেক স্বাধীন বাদশাহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। আর এসকল যুদ্ধের বিশাল খরচ বহন করার জন্য অপর কোনো রাজ্য থেকে ঋণ করার প্রয়োজন হতো। কিন্তু এক রাজ্য অপর রাজ্যকে এত বড় পরিসরে ঋণ দিতে রাজি হতোনা। কারণ এতে একদিকে যেমন বিপরীত রাজ্যের তোপের মুখে পড়ার আশঙ্কা থাকতো, অন্যদিকে থাকতো ঋণদাতা রাজ্যের যুদ্ধের সময় ঋণী হয়ে যাওয়ার ভয়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রকে এত বড় ঋণ দেওয়ার সামার্থ্য শুধু পুঁজিবাদি মহাজন, সুদখোর আর জুয়াড়িরদেরই ছিলো। ব্যাংক(২) সিস্টেমের বদলে প্রচুর সোনা এই সুদি মহাজনদের কাছে জমা থাকার কারণে তারাও আরো বেশি সুদে রাজাদের ঋণ দিতে চাইতো। চড়ামূল্যের এইসব সুদি ঋণ শোধ প্রায় সময়েই সম্ভব হতোনা রাজাদের জন্য। ঋণের চাপে সমাজের কিছু মানুষের করায়ত্বে চলে আসতো বাদশাহরা। আর এভাবে প্রত্যেক রাজ্যের মধ্যেই পুঁজিবাদি শ্রেণীর ক্ষমতা পাকপোক্ত হতে লাগলো।
সপ্তদশ শতাব্দীতে খ্রিস্টানরা পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থার এই একচেটিয়া ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরতে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। ইংল্যান্ডের সামরিক প্রধান ক্রেমওয়েল আর সুইজারল্যান্ডের জঁ ক্যালভা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এই রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্য পুঁজিবাদকে পূর্ণনিয়ন্ত্রণ নয়, বরং পুঁজিবাদের পরিধি ঠিক করে দিয়ে তাকে ধর্মের ব্যাখ্যার আলোকে প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য সুইজ্যারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড উভয় রাষ্ট্রেই সুদভিত্তিক সমাজ গ্রহণ করে নেওয়া হয়। যে নিয়ম-কানুনকে আজ আমরা ইসলামি ব্যাংক বলি, তার সূচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর খ্রিস্টান অর্থনীতি ও ধর্মীয় আলোচনায় পাওয়া যায়। জঁ ক্যালভা আর ক্রেমওয়েল চেয়েছিলো পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থাকে খ্রিস্টান ধর্মের আলোকে সাজাতে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। কেননা পুঁজিবাদ তার স্বভাবনুযায়ী একটি খোদাদ্রোহী জীবনব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তিমানব বা হিউম্যান বিয়িং নিজের প্রভুত্বের প্রকাশ করে থাকে। পুঁজিবাদ কখনোই কোনো ধর্মের আধিপত্য নিজের ভিতর মেনে নেয় না। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো এই কাজটাই আজকের ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামি গণতন্ত্রের ধারকবাহক ও মুসলিম সমাজের এক শ্রেণির কর্তাগণ করে যাচ্ছে।
একনায়কতান্ত্রিক বাদশাহি শাসন ব্যবস্থায় যদিও ধর্মীয় অনেক বিষয় সীমাবদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু এমন রাজ্যেও পুঁজিবাদ তার পূর্ণবিকাশ করতে পারে না। কেননা, একনায়কতন্ত্র এই বাদশারাও সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতিকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মাঝেই নিহিত মনে করে। এবং তারা নিজেদেরকে খোদার একমাত্র প্রতিনিধি ভাবে।
পুঁজিবাদের সকল তাত্ত্বিকগণ এই ব্যপারে একমত যে, পুঁজিবাদের বিপ্লবের পূর্ণতার জন্য শুধু প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। চাই সে প্রজাতন্ত্রে উদারপন্থি পুঁজিবাদ পদ্ধতি পরিচালিত হোক, বা সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। জাতিগত উন্নতির স্বার্থে পরিচালিত হোক, বা ব্যক্তিস্বার্থে।
সপ্তদশ শতাব্দীর পরে পৃথিবীতে বেশকিছু পুঁজিবাদি বিপ্লব হয়েছে। যার মাধ্যমে শক্তিশালী অনেকগুলো পুঁজিবাদি রাষ্ট্র অস্তিত্বে আসে। সর্বপ্রথম সফল বিপ্লব হয় ১৬৮৮সনে ইংল্যান্ডে। যাকে গৌরবময় বিপ্লব (Gloirous Revoluion) বলা হয়। এরপর পুঁজিবাদের একের পর এক সফল বিপ্লব হতে থাকে। তার একটি সূচি নিচে দেওয়া হলো—
• ১৭৭৬ এবং ১৮৬৩ সালে আমেরিকান বিপ্লব।
• ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব।
• ১৯১৭ এবং ১৯৯১ সালে রুশ বিপ্লব।
• ১৯৩৩ সালে জার্মানে ফ্যাসিবাদের বিপ্লব।
• ১৯৪৯, ১৯৬৬ সালে এবং ১৯৭৬, ১৯৭৯ সালে চীনা কমিউনিস্ট বিপ্লব।
• ১৮০৯ থেকে ১৮২৪ ল্যাটিন আমেরিকান বিপ্লব।
• উপনিবেশবাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিপ্লব—ভারতে ১৯৪৭ সালে, ইন্দোনিশিয়ায় ১৯৪৯ সালে, মিশরে ১৯৫৪ সালে, আফ্রিকায় ১৯২০ সালে।
এই প্রতিটি বিপ্লবের ফলাফল ছিলো, সব স্থানেই শক্তিশালী পুঁজিবাদি শাসন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকা প্রতিষ্ঠা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত (১৯৪৫) শক্তিশালী পুঁজিবাদি রাষ্ট্রগুলোর মাঝে পরস্পর যুদ্ধ লেগে ছিলো।
১৯৪৫ সালে পুঁজিবাদি জাতিরাষ্ট্রগুলো আমেরিকার সামরিক ও রাজনৈতিক সর্বকর্তৃত্ব (হাকেমিয়্যাত) স্বীকার করে নেয়। এরপর উন্নত পুঁজিবাদি জাতিরাষ্ট্রগুলো অনুন্নত পুঁজিবাদি রাষ্ট্র, যেমন ভিয়েতনাম, ইরাক, সার্বিয়া এবং অপুঁজিবাদি সংগঠন, যেমন, আলকায়েদা, তালেবান, হামাস—এদের বিজিত অঞ্চলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কখনোই উন্নত পুঁজিবাদি রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মাঝে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না। আমেরিকা ও সোভিয়ত ইউনিয়নের মাঝে কোল্ডওয়ার হয়, কিন্তু কখনোই সশস্ত্র যুদ্ধ ঘটেনা। চীন আমেরিকার সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক বিনিয়োগ লগ্নিকারী দেশ। হাজারা কোটি মার্কিন ডলার চীন আমেরিকার ফেডেরাল সোসাইটিগুলোতে (US Federeal Securities) পুঁজিলগ্নি করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলো ও ভারত আমেরিকার সবচেয়ে নিকটতম বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় এরা কোনো কমতি রাখেনি। কতক পুঁজিবাদি চিন্তাবিদদের ধারণা হলো, শক্তিশালী পুঁজিবাদি জাতিরাষ্ট্রগুলোর মাঝে এরকম পরষ্পর সহযোগিতা এই কথারই প্রমাণ বহন করে যে, আমরা বর্তমানে পুঁজিবাদি ইতিহাসের এক নতুন সময়ে উপনীত হয়েছি, যাকে ‘গ্লোবালাইজেশনের’ যুগ বলা হয়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুঁজিবাদি পৃথিবী দুই তাবুতে ভাগ হয়ে যায়। এক অংশের নেতৃত্ব ছিলো সোভিয়ত ইউনিয়ন। যারা পুঁজিবাদের উন্নতির মাধ্যম সমাজতন্ত্রকে মনে করতো। আর দ্বিতীয় অংশে ছিলো আমেরিকা। যারা উদারনৈতিক পুঁজিবাদকে পুঁজিবাদ বিস্তারের সঠিক মাধ্যম মনে করতো। আমেরিকা সমাজতন্ত্রের প্রভাব পৃথিবী থেকে দূর করতে দুটো চুক্তি সম্পাদন করে।
• ন্যাটো ও তার মিত্র সামরিক শক্তিশালী সংগঠন প্রতিষ্ঠা। যা সকল উদারনৈতিক পুঁজিবাদি রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে আমেরিকার হাতের পুতুলে পরিণত করেছে। আর আমেরিকা উদারনৈতিক পুঁজিবাদের সংরক্ষণ ও উন্নতির সামরিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।
• বেটন ওডস চুক্তি। যার অধীনে গৃহিত হয়—
ক. আমেরিকার ডলার পৃথিবীর একমাত্র কারেন্সি হবে যার মাধ্যমে স্বর্ণের বিনিময় হার (exchange rate) নির্ধারণ করা হবে। এবং এই বিনিময় মূল্যের মাঝে কোনোরকম পরিবর্তন আসবে না। আমেরিকা এই দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, যখনই অন্যকোনো রাষ্ট্র সোনা দাবি করবে তখন আমেরিকা ৩৫ ডলারের বিনিময়ে এক আউন্স স্বর্ণ তাকে দিতে বাধ্য থাকবে। এবং এই পরষ্পর বিনিময় হার অপরিবর্তনীয় থাকবে।
খ. প্রতিটি দেশ তাদের দেশীয় মুদ্রা আমেরিকার ডলারের সাথে বিনিময় হার নির্ধারণে আইএমএফ-এর মধ্যস্থতার মাধ্যমে করতে হবে। আইএমএফের মধ্যস্থতা ছাড়া মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করার অধিকার কারো থাকবে না।
গ. আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হবে যা বৈশ্বিক অর্থনীতির একমাত্র বৈধ প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত হবে।
১. আইএমএফ(IMF)। যার কাজ হলো বিশ্বের বিভিন্ন পরস্পর লেনদেনের মাঝে সমতা ঠিক রাখা। ২. বিশ্বব্যাংক (World Bank) যার কাজ হলো বিশ্বে পুঁজিবাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করা। ৩.আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization)। যার কাজ হলো আন্তর্জাতিক সংলাপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির পথে বিঘ্নতা সৃষ্টিকারী সকল সমস্যার সমাধানে যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাওয়া।
এই চুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি চুক্তিকারী রাষ্ট্রের এই অনুমতি ছিলো যে, তারা নিজেদের মুদ্রার মান নিজেরাই আমেরিকায় স্বর্ণ জমা দিয়ে কম-বেশি করতে পারবে।(৩)
১৯৭৩ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান নিকসন ডলার আর স্বর্ণের এই বিনিময় নির্ধারণ ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেয়। কেননা ভিয়েতেনামের যুদ্ধে বিশাল খরচের কারণে আমেরিকা ৩৫ ডলারের বিনিময়ে অন্যরাষ্ট্রগুলোকে এক আউন্স স্বর্ণ প্রদানে অক্ষম হয়ে যায়। এরপর থেকে আজ অব্দি কোনো দেশের মুদ্রার বিপরীত কোনো স্বর্ণ, রূপা বা অন্য সম্পদ নেই। তাই প্রতিটি দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্য সেদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে দেয়, অথবা আন্তর্জাতিক মুদ্রা মার্কেটে স্বাধীন লেনদেনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।
১৯৮০ দশকের পরে আন্তর্জাতিক লেনদেনে পুঁজিবাদের উপর রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ কমতে থাকে। আর সুদ ও শেয়ার মার্কেটের বাজার এমনভাবে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, তার পরিধি দ্রুত পুরো পৃথিবীকে গ্রাস করে নিতে লাগলো। রাষ্ট্রের বিধিনিষেধ দ্রুত কমে যাওয়াতে পুঁজিবাদের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন হয়ে গেলো—এখন অধিক থেকে অধিক লাভের জন্য ইচ্ছেমতো রাষ্ট্রীয় সীমানা সে পার হতে পারে। অর্থাৎ, পুঁজিবাদ এখন গ্লোবালাইজ হয়ে গেলো।
পুঁজিবাদকে গ্লোবালাইজেশন করতে ইন্টারনেটের আবিষ্কারও অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। আমেরিকার সেনাবাহিনীর প্রধান প্রতিষ্ঠান ইউএস ডিপার্মেন্ট অফ ডিফেন্সের (US Department of Defence) ইন্টারনেট তৈরি করা। যা ১৯৯০ দশকে কমার্শীয়াল করে দেওয়া হয়েছে। নেটের মাধ্যমে খবরাখবর আদানপ্রদান অনেক দ্রুততার সাথে করা সহজ হয়ে গেলো। আর এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদের কার্যকরিতাকে আরো উন্নতিতে পৌঁছে দিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখে।
এই সবকিছুর ফলাফল দাঁড়ালো, পুঁজিবাদি মালিকানা পূর্ণ শক্তিশালী হতে লাগলো। পুঁজিবাদি মালিকানা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ সমস্ত সংগঠন, যেখানে সম্পদের ব্যবহারের অধিকার শুধু সেসমস্ত ব্যক্তিদেরই দেওয়া হয়, যারা এই সম্পদ ব্যবহার করে আরো অধিক সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা রাখে। আর এমন লোকদের ম্যানেজমেন্ট বলা হয়। এরা সম্পদের প্রকৃত মালিক নয়। কিন্তু সম্পদের অগাধ ব্যবহারের অধিকার পুঁজিবাদি ব্যবস্থা তাদের দিয়ে রাখে। পুঁজিবাদি সম্পদের আইনত মালিক নিজের সম্পদ ব্যবহার করতে পারে না। তারা শুধু লাভ (Dividend) অর্জন করতে পারে অথবা নিজের শেয়ার বিক্রি করে মূলধন (Capital Gain) অর্জন করতে পারে।
পণ্যের মার্কেট, মুদ্রা মার্কেট, শেয়ার মার্কেট—সব সম্পদ এভাবে হাতেগোণা কিছু কর্পোরেশনের হাতে চলে যায়। তারাই বস্তুর মূল্য, পুঁজিবাদি লেনদেন আদানপ্রদানের নীতি নির্ধারক ও কর্তা বিবেচিত হয়। একনায়কতান্ত্রিক এই কর্পোরেশনের সামনে জাতিরাষ্ট্রের শাসকরা নিত্যদিন অসহায় হয়ে যাচ্ছে।
পুঁজিবাদের উপর জাতিরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে জাতিসঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রয়েছে । জাতিসংঘের অধীনে দুটো সংগঠন রয়েছে। ১. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization)। দুই. বিশ্ব কৃতিস্বত্ব কর্তৃপক্ষ (World intrellectual Property organization)। যারা পুঁজিবাদি সম্পদকে ব্যাপক করার জন্য এমন উপযোগী নিয়ম তৈরি করে, যেগুলোর মাধ্যমে সরকারি মালিকানা লেনদেন, তথ্য আদান-প্রদান করার ক্ষমতা সীমিত হতে লাগলো। WIPO-এর করা আইনগুলোর বাস্তবায়ন সঠিকভাবে করতে আরো কিছু কোম্পানীও আন্তর্জাতিকভাবে তৈরি করা হলো যাদের কাজ শুধু এই বিষয় তদারকি করা যে, সরকার ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানীগুলো আন্তর্জাতিক এই নিয়মগুলো কতটুকু মেনে চলছে। এই কর্পোরেশনগুলোকে রেটিং এজেন্সি (Ratnig agencies) এবং স্ট্যান্ডার্ডস সেটিং অরগানাইজেশন (Standard setting Agencies) বলা হয়। যা ISC এবং IAS নামে পরিচিত।
এসমস্ত বৈশ্বিক সংগঠনের পর্দার আড়াল থেকে পৃথিবীব্যাপি পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করে চলছে একদল পুঁজিপতিরা, যা মানুষের আখিরাতকেই শুধু শেষ করে দিচ্ছে না, দুনিয়াকেও ধ্বংসের দাঁরপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। তাই পুঁজিবাদের নিরেট ইতিহাসের সাথে পুঁজিবাদের মৌলিক দর্শন ও সে দর্শনের আলোকে তার কর্মপ্রদ্ধতিগুলোর সঠিক অনুধাবন করাও সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ।
২.১ পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট
পুঁজিবাদ ঐ জীবনব্যবস্থাকে বলা হয়— যেখানে হিংসা ও লিপ্সাকে বিবেক সম্মত মনে করা হয়। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি পুঁজিবাদি, যার জীবনের উদ্দেশ্য শুধুই দুনিয়াতে নিজের কামনা-বাসনা পূর্ণ করা। একেই বলা হয় স্বাধীনতা। আর স্বাধীনতার এই সংজ্ঞাই হলো পুঁজিবাদি ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। একজন পুঁজিবাদের জীবনের উদ্দেশ্য, নিজের স্বাধীনতার উন্নতিকে পূর্ণতায় পৌঁছানো, যাতে দুনিয়ার সকল শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে নফসের সমস্ত চাহিদা ও কামনাবাসনা পূর্ণ করা যায়। আর পুঁজিবাদি যুক্তিতত্ত্ব মানুষকে এই উদ্দেশ্য অর্জনের পথ দেখিয়ে দেয়। এই যুক্তিতত্ত্বের মৌলিক দাবি এটাই—মানুষের মাঝে এই যোগ্যতা আছে, সে দুনিয়ার সকল শক্তিকে নিজের মনোবাসনা পূরণের মাধ্যম বানাতে পারবে। পুঁজিবাদি যুক্তিতত্ত্ব অতিপ্রাকৃতিক যে ধারণাগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত তাই হলো পুঁজিবাদের মৌলিক আকিদা। আর এই আকিদার কালেমা হলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল ইনসান’ মানুষই একমাত্র সত্ত্বা যে পূজার উপযুক্ত। আর পুঁজিবাদি ব্যক্তি সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই কালেমার উপর ঈমান আনা অত্যান্ত জরুরি। এই আকিদা প্রকাশ করতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাকে পুঁজিবাদি সমাজ বা ‘সোল-সোসাইটি’ বলা হয়। সোল-সোসাইটিতে হিংসা ও লিপ্সাই মানুষের পারস্পরিক কাজের সীমানা ঠিক করে। আর এই হিংসা ও লিপ্সাকে বিবেকসম্মত মনে করা ব্যক্তিকেই বলা হয় হিউম্যান বিয়িং। প্রসিদ্ধ ফ্রেন্স দার্শনিক মিশেল ফুঁকোর বক্তব্যনুযায়ী হিউম্যান বিয়িংয়ের ধারণা সর্বপ্রথম সপ্তদশ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়। যা খ্রিস্টান ধর্মে মানবজাতির (mankind) ধারণাকে বাতিল বলে ঘোষণা করে।
হিউম্যান বিয়িং বা ব্যক্তি মানব হলো সে মানুষ যে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল ইনসান’ এই কালিমার উপর ঈমান এনে নিজেকে নিজের স্রষ্টা, স্বনির্ভর ও সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী এক সত্তার ঘোষণা করে। এবং স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে সে স্বস্রষ্ট্রা সত্তার বিকাশের জন্য সংগ্রাম করে যায়। এই সংগ্রামে সে অন্য হিউম্যান বিয়িংয়ের সাথে সম্পর্ক এই ভিত্তিতে ঠিক করে যে, স্বাধীনতা অর্জনের এই সংগ্রামে তারা এক অপরের সহযোগী হবে। এক হিউম্যান বিয়িং অপর হিউম্যান বিয়িংকে নিজের উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম মনে করে। আর অপরের উদ্দেশ্য অর্জনের সাহায্য করতে সে এই শর্তে রাজি হয়, এভাবে সাহায্যের দ্বারা সে নিজের স্বাধীনতাকে আরো উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারবে। নিজেদের পারস্পরিক এই কর্মকাণ্ডের প্রাতিষ্ঠানিক রূপকেই মার্কেট বলা হয়। মানুষের মাঝে পরস্পর যত সম্পর্ক থাকে পুঁজিবাদি সমাজে ধীরে ধীরে সেগুলোতে মার্কেট(৪) প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মানুষ যত ব্যক্তিমানবে পরিণত হতে থাকবে ততই তাদের মাঝের পরস্পরের সম্পর্ক মার্কেটাইজ হতে থাকবে। ভালোবাসা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বা ধর্মীয় ঐক্যবদ্ধতা—এসকল সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সমাজের পরিধি পুঁজিবাদি সমাজ ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। এক পর্যায়ে তা ‘নাই’-এর স্থরে চলে যাবে। প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী কার্ল পোলানি (Karl Polanyi) লেখে, সমাজে মানুষের মাঝে যত ধরণের সম্পর্ক হয় এমন সমস্ত প্রতিষ্ঠান পুঁজিবাদি মার্কেট গ্রাস করে নেয়। মার্কেটব্যবস্থা বংশ, গোত্র, ইবাদতের স্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, শরীর চর্চাকেন্দ্র এমনকি শাসন ব্যবস্থাকেও পুঁজিবাদের উপনিবেশে পরিণত করে।
পুঁজিবাদি সমাজ, বিশেষত মার্কেটের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনে একটি নির্দিষ্ট ধরণের ‘রাষ্ট্র’-এর প্রয়োজন হয়। যে রাষ্ট্রকে পুঁজিবাদের ভাষায় প্রতিনিধিত্বমূলক প্রজাতন্ত্র (Reperesenative Republic) বলা হয়। অপুঁজিবাদি রাষ্ট্রও রিপাবলিক হতে পারে, তবে তাতে জনগণের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয় না। এই প্রতিনিধিত্বমূলক প্রজাতন্ত্র (Reperesenative Republic) সামাজিক চুক্তির (Social Contract) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সেই সামাজিক চুক্তির বাস্তববিক রূপটিই হলো প্রতিটি পুঁজিবাদি দেশের সংবিধান। শাসন পরিচলনার এই সংবিধানে কিছু বিষয়ের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকতে হয়—
• এই শাসন ব্যবস্থা হিউম্যান বিয়িংয়ের স্বাধীনতাকে উন্নতি করার মাধ্যম হবে। আর এটাই পুঁজিবাদি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের লক্ষ্য।
• ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিধিকে এমনভাব সাজাতে হবে, যাতে এই স্বাধীনতা সকলের ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতার পথকে উন্নত করে।
• সংবিধান একজন মানুষকে ব্যক্তিমানব বা হিউম্যান বিয়িং বানানোর জন্য ঐ সকল দায়িত্ব অপরিহার্যভাবে আদায় করবে, মার্কেট যেগুলো করতে অক্ষম। এর মাঝে বিশেষ হলো পুঁজিবাদি শিক্ষাব্যবস্থার ব্যপক প্রচলন ঘটনো, এবং পুঁজিবাদের কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার পথে যত বাঁধা তা দূর করা।
২.২ পুঁজিবাদের ভুল মূল্যায়ন
পুঁজিবাদ শুধুই একটি অর্থনৈতিক দর্শন নয়। তার রয়েছে নিজস্ব ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় দর্শন। পুঁজিবাদি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র—এসকলের মাঝে একটি জৈবিক সম্পর্ক রয়েছে। এটা সম্ভব নয়— পুঁজিবাদি ব্যক্তিত্ব অ-পুঁজিবাদি সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আবার এটাও সম্ভব নয়— ইসলামি ব্যক্তিত্ব কোনো পুঁজিবাদি সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রাধ্যন্য বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়াবে।
কিছু দাওয়াতি সংগঠন, আলেমগণ ও ইসলামি রাজনৈতিক দলের সদস্যরা পুঁজিবাদি ব্যক্তিত্ববোধকে সমাজ থেকে মূলোৎপাটনে দাওয়াতি ও বুদ্ধবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে। অথচ পুঁজিবাদি সমাজ ও পুঁজিবাদি রাষ্ট্রের মূলোৎপাটনের প্রচেষ্ঠাকে অগুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এবং এ ধরণের সকল কার্যক্রমের সাথে কোনোরকম সম্পর্কও তাদের থাকে না! এটা পুঁজিবাদ সম্পর্কে তাদের উপরের ভুল ধারণার ফল—পুঁজিবাদি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সব আলাদা আলাদা বিষয়।
আমি এটা বলতে চাই না যে, সকল ইসলামি রাজনৈতিক ও দাওয়াতি সংগঠন নেতাদের সকল কার্যক্রম শুধু পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থার মূলোৎপাটনে ব্যয় করুক। বরং পুঁজিবাদের ধ্বংসসাধনে বিভিন্ন ইসলামি দলের পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিজেদের সু-সম্পর্ক সৃষ্টি করাকে আমি একান্ত জরুরি ও আবশ্যক মনে করি।
অন্যদিকে কিছু আলেম পুঁজিবাদকে একটি জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনে করেন না। যার ফলে এই জীবন ব্যবস্থার মধ্যেই ‘ইসলামি ব্যাংক’, ‘ইসলামি গণতন্ত্র’-এর মাধ্যমে পুঁজিবাদি জীবন ব্যবস্থাকে জোড়াতালি দিয়ে ইসলামিকরণের বিভিন্ন হিলা ও প্রস্তাব তারা পেশ করে থাকে। আর এ ধরণের চিন্তারও মৌলিক কারণ হলো পুঁজিবাদি ব্যক্তি, পুঁজিবাদি সমাজ ও পুঁজিবাদি রাষ্ট্র—এসবকিছুর পরস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে অজ্ঞতা।
পুঁজিবাদ একটি জীবন দর্শনের নাম। তবে তার রয়েছে বহু মতাদর্শ। যেমন, উদারনৈতিক পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, সোশ্যাল-ডেমোক্রেসি, জাতীয়তাবাদ এবং পোষ্ট-মর্ডানিজম ইত্যাদি। এই সবগুলোই পুঁজিবাদি দর্শন থেকে সৃষ্ট। কেননা সবগুলোই মৌলিকভাবে পুঁজিবাদের অতিপ্রাকৃতিক যে-সকল ধারণা, সেগুলোর উপর বিশ্বাস রাখে। এসকল মতাদর্শের কালিমা হলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল ইনসান’ এবং এসকল মতাদর্শের একটিই চেষ্টা—মানুষকে ব্যক্তিমানব তথা হিউম্যান বিয়িং বানানো। স্বাধীনতা, সাম্য ও উন্নতি; এই তিন নীতির উপর সৃষ্ট হিউম্যান তৈরি করাই এমতবাদগুলোর উদ্দেশ্য। এসকল মতাদর্শের সম্মেলিত দাবি হলো, মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা (Self Creator), স্বনির্ভর ও স্বায়ত্ত্বশাসিত একসত্তা। তাই সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানের পরম উদ্দেশ্য হলো—মানুষের হিউম্যান বিয়িং হওয়ার পথ চলাকে উন্নতির সকল ব্যবস্থা করে দেওয়া। তা ভিন্ন আর কিছুই নয়।
এই মতাদর্শগুলোর মাঝে পরস্পরিক যে মতানৈক্য, তা ‘উদ্দেশ্য’ নিয়ে নয়, বরং উদ্দেশ্য অর্জনের পথ কোনটি, তা নিয়ে। পুঁজিবাদি ব্যক্তি, সমাজ, ও রাষ্ট্র গঠনে উন্নত, ফলপ্রসূ ও সঠিক পদ্ধতি কোনটি হবে তা নিয়ে এই মতাদর্শগুলো মতানৈক্যে লিপ্ত হয়।
লিবারিজমে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি স্বাধীনতাকে উন্নত থেকে উন্নতর করা। সমাজতন্ত্রের দাবি হলো, পুঁজিবাদি রাষ্ট্রগঠনের উদ্দেশ্য শ্রমিক শ্রেণির (Proletariat) স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। কেননা হিউম্যান বিয়িং হওয়ার আসল প্রতিনিধি এই শ্রণিই। এবং এদের একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সামাজিকভাবে মানুষের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। সোশ্যাল-ডেমোক্রেসিদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উদারনৈতিক ব্যক্তি স্বাধীনতার মাঝে সমন্বয় সাধন করা। পোষ্ট-মর্ডানিষ্টরা স্বাধীনতাকে শুধুমাত্র নান্দনিকতত্ত্বের (Aesthetic) ভিত্তিতে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তাদের মত হলো প্রতিটি সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন মানুষের স্বাধীনতাকে কোনো না কোনোভাবে সীমাবদ্ধ করে দেয়। তাই সব ধরণের নিয়মের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে যেতে হবে।
এইসকল মতাদর্শগুলোর মতানৈক্য থেকে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, পুঁজিবাদি জীবন ব্যবস্থা ঐসকল মতদর্শ কেন্দ্রিক ভিন্নতা গ্রহণ করে নিতে পারে, যেগুলো পুঁজিবাদি জীবন ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-মাধ্যম মাত্র।
মোটকথা, পুঁজিবাদের দর্শন মূলগতভাবেই একটি খোদাদ্রোহী দর্শন, যাকে ইসলামের সাথে খাপ খাওয়ানোর কোনো সুযোগ নেই। তাই এই দর্শনের সর্বরকম মোকাবেলা করা মুসলিমদের আবশ্যকীয় একটি দায়িত্ব।
৩. পুঁজিবাদের কর্মপদ্ধতি
পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থা অনন্তকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত কোনো জীবনব্যবস্থা নয়। দুনিয়ার বয়স আনুমানিক সারে পাঁচ হাজার বছর হবে। এর মাঝে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব আসে সর্বোচ্চ সাতশত বছর পূর্বে। তার মধ্যেও আনুমানিক চার থেকে পাঁচশত বছর পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থার পরিধি একবারে নির্দিষ্ট ছিলো। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশ শতকের শুরু থেকে, যা আজ পর্যন্ত তার পরিব্যপ্তি বৃদ্ধি করে চলছে। যে বিশ্বাস আর দর্শনের উপর পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত (হিউম্যান বিয়িংয়ের উলুহিয়্যাত, পৃথবীর চিরস্থায়ীত্ব), তা যুক্তির আলোকে প্রতিষ্ঠিত কোনো মত নয় বরং অতিপ্রাকৃতিক কিছু ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা খণ্ডনে আকল ও বিবেক কোনোটাই অক্ষম নয়। আর আসমানী ওহি তো এই বিশ্বাসগুলোর ভ্রান্তি স্পষ্ট ঘোষণা করে।
পুঁজিবাদের ইতিহাসকে সঠিক করে বললে ‘জন্মগত সংকট’-এর ইতিহাস বলা যাবে। অর্থনীতির একটি থিউরি (Business Cycle theory) এই অস্পষ্টতাকে সঠিকভাবে বর্ণনা করার জন্য গঠন করা হয়েছে।
ঐ থিউরি অনুযায়ী—
• পুঁজিবাদি অর্থনীতিতে সর্বদা সম্পদ সমান গতিতে বৃদ্ধি পাবে— এটা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় কোনো বিষয় নয়। বরং লাভ হবে, কখনো ঘাটতি হবে।
• উদপাদন আর ঘাটতির চলমান পক্রিয়া কখনো দীর্ঘ সময়ে দেখা দিবে কখনো অল্প সময়ে। পুঁজিবাদি অর্থনীতি ব্যবস্থা সর্বদা অস্থিতিশীল থাকে। উৎপাদন পরিবর্তনের সাথে সাথে আমদানি-রফতানি, ইনকাম, বিনিয়োগ, সঞ্চয় বা আন্তর্জাতিক ব্যবসা, সবকিছুর মাঝেই উত্থান-পতন শুরু হয়ে যায়। যার কারণে মুদ্রা মার্কেট, শেয়ার বাজারে ব্যাপক প্রভাব পড়ে।
পুঁজিবাদি উৎপাদনে উত্থান-পতনের কয়েকটি যুগ—
• সমৃদ্ধি (Expansion) ; যখন সামষ্টিকভাবে সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটা উন্নত পুঁজিবাদি রাষ্ট্রগুলোতে ১৯৫০ ও ১৯৬০ সালে দেখা গেছে।
• সমৃদ্ধি (Expansion) যখন তা পূর্ণ উৎকর্ষতায় থাকে। যা ১৯৬০ সালের শেষের দিকে দেখা গিয়েছে।
• মন্দার (Reccesion) সময়। যখন সম্পদের উৎপাদন ঘাটতির দিকে থাকে, বেকারত্ব বাড়তে থাকে। যেমনটা ১৯৭৯-এর দশকে হয়ছিলো।
• মন্দার (Reccesion) সবচেয়ে খারাপ সময়, যা ১৯৮০-এর শুরুর দিকে দেখা যায়।
• এরপর আবার সমৃদ্ধির সময় শুরু হয়। যা ১৯৯০-এর দশকে বেশি অংশ জুড়েই ছিলো।
• ২০০১-এর পর উন্নত পুঁজিবাদি রাষ্ট্রগুলো মন্দার কবলে পড়ে। ২০০৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত মন্দার এই অবস্থা একেবারে নিম্মমুখী হয়ে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থনীতি সংকটে পড়ে যায়।
• আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্য হলো, ২০১০-এর দশকে আবার সমৃদ্ধির (Expansion) সময় শুরু হয়েছে। কিন্তু অনেক অর্থনীতিবিদদের মত হলো, এই তথ্য সঠিক নয়। বরং এই দশকে পুঁজিবাদ আরো অধিক সংকটে রয়েছে।
পুঁজিবাদের সংকট কী? পুঁজিবাদের সংকট বুঝার জন্য বিভিন্ন বস্তু ও ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের পরস্পরিক সম্পর্ক বোঝা অত্যন্ত জরুরি।
ফাইন্যান্সের মার্কেট দু’ধরণের হয়। ১. মুদ্রা মার্কেট। ২. শেয়ার মার্কেট।
মুদ্রা মার্কেট ব্যাংকের মাধ্যমে সমাজের সকল সম্পদগুলোকে এক স্থানে জমা করে। তারপর সে সম্পদ দিয়ে পুঁজিবাদি মুদ্রা সৃষ্টি করে। এবং সুদি চুক্তি ও লেনদেনের মাধ্যমে এই সম্পদ সমাজের শুধু ঐ শ্রেণির নিকট অর্পন করে, যারা এই পুঁজিকে দ্রুত থেকে দ্রুত বৃদ্ধি করার সক্ষমতা রাখে।
আর শেয়ার মার্কেট সম্পদের নিরাপত্তাকরণের (securitisation)-এর মাধ্যমে পুঁজিবাদি শেয়ার প্রতিষ্ঠা করে। পুঁজিবাদি শেয়ার কারো মালিকাধীন শেয়ার নয়। তা হলো ঐ সমস্ত শেয়ার—
• যার মূল্য ডাইরেক্ট বা ইন-ডাইরেক্ট শেয়ার মার্কেটে নির্ধারণ হয়, অথবা পুঁজিবাদি রাষ্ট্রের শোষণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
• যার ব্যবহারের একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো পুঁজিবাদের উন্নতিতে বৃদ্ধিসাধন করা।
উন্নত পুঁজিবাদি সমাজে পুঁজিবাদ সুদ ও শেয়ার মার্কেটের মাধ্যমেই অর্থনীতির বাগডোর নিজের হাতে নিয়ে আসে। আর এ কাজ বিভিন্ন কোম্পানী তৈরি করার মাধ্যমে করে। একটি সাধারণ কোম্পানিতেও হাজারো আইনসম্মত মালিক থাকে। যেহেতু একটি কোম্পানীর সম্পদ (Bond) শেয়ার মার্কেটে প্রতি মুহুর্তে ক্রয়-বিক্রয় হতে থাকে, তাই কোম্পানীর আইনগত মালিকও প্রতি মুহুর্তে পরিবর্তন হতে থাকে। কোম্পানির এই আইনত মালিকদের কোম্পানী পরিচালনায় কোনোরকম অংশগ্রহণ থাকেনা। যেমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একজন ভোটারের ভোট দেওয়ার পর রাষ্ট্রের কার্যক্রমের দখল দেওয়ার কোনো অধিকার থাকে না। বছরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভায় (Annaul General Meeting) আইনত এই মালিকদের অল্প সংখ্যক কিছু ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পরিচালনা পরিষদের কার্যক্রম সঠিকভাবে চলছে—এই বিষয়ে সত্যায়ন করে আসে। কোম্পানীকে শুধু তারাই পরিচালনা করতে পারে যাদের এই বিষয়ে পূর্ণ দক্ষতা রয়েছে—কিভাবে কোম্পানীর সম্পত্তিকে ব্যবহার করে দ্রুত থেকে দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারবে। বাস্তবতা হলো পুঁজিবাদি শেয়ারের মালিক একমাত্র পুঁজিবাদ (হিংসা ও লিপ্সা) নিজেই হয়ে থাকে। আর বাকি সকল শুধু আইনত মালিক। আর কোম্পানির মেনেজম্যান্ট, কর্মকর্তা এবং ব্যবস্থাপক—এরা শুধুই পুঁজিবাদের গোলাম। এই শ্রেণির কারোই এই বিষয়ের ইখতিয়ার থাকে না, কোম্পানীর সম্পদকে পুঁজি বৃদ্ধির বদলে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। যদি কেউ এমন দুঃসাহস করে তাহলে কোম্পানী শেয়ার মার্কেটে একদম দেউলিয়া হয়ে যাবে, শেয়ারের দাম শেষ হয়ে যাবে—এক কথায় পুরো কোম্পানী বরবাদ হয়ে যাবে।
পুঁজিবাদের সংকট ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট থেকে নিয়ে পুরো অর্থব্যবস্থায় ছড়িয়ে পড়ে। পুঁজিবাদের সংকট বুঝার কয়েকটি আলামত রয়েছে।
• মুদ্রার দ্রুত দরপতন হতে থাকবে, বিপরীতে পণ্যের মূল্য দ্রুত উর্ধ্বগতিতে বাড়তে থাকবে।
• শেয়ারের মূল্য ধারণাতীত পড়ে যাবে আর জমাকৃতমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এতে শেয়ার বাজারে কোম্পানীগুলো পুরোদমে দেওলিয়া হতে থাকবে।
• বড় বড় ব্যাংকগুলো ধ্বংস, দায়িত্ব আদায়ে অপারগতা, বেপরোয়াভাবে কমে যাবে। এবং যেই যে সম্পদগুলোর মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছিলো তা বড় পরিসরে বাজেয়াপ্ত করা হবে।
• বড় পরিসরে ব্যবসায়িক লস ও পণ্যের বাজারে, ক্রয়-বিক্রয়ে অসফলতা বাড়তে থাকবে।
• ব্যাপক হারে দেশের বেকারত্ব বাড়তে থাকবে ও আমদানী কমতে থাকবে।
পুঁজিবাদের সংকট বিভিন্ন রকমের হয়। এমন নয় যে, উপরের সবগুলো আলামতগুলো কোনো একটি সংকটের মধ্যে একসাথে দেখা দিবে।
যেমন, ২০০৭ বা ২০০৮ সালে আমেরিকায় যে সংকট দেখা দিয়েছে তা আমেরিকান কারেন্সির সংকট ছিলো না। তা আমেরিকার ব্যাংকিং খাতে তারল্যের সংকট ছিলো। সেই সংকট আমেরিকার শেয়ার বাজারে কোনো প্রভাব ফেলেনি। (শুধু ব্যাংগুলোর যে শেয়ার ছিলো সেগুলোর দরপতন হয়) এমনকি এতে সরকারের জনপ্রিয়তাও কোনোরকম হ্রাস পায়নি। বিপরীতে ২০০৯, ২০১০ সালে ইউরোপে যে সংকট দেখা দেয় তাতে গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল ও ইটালীর সরকার পর্যন্ত কেঁপে উঠে। ব্রিটিশ ও আমেরিকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে হাজার কোটি ডলার খরচ করে ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানীগুলোকে সে যাত্রা রক্ষা করে। গ্রিস আর পর্তুগালের এমন সামর্থ না থাকার কারণে আইএমএফ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জার্মানীর থেকে চড়ামূল্যে ও কঠিন শর্তে ঋণ নিতে বাধ্য হয়।
তবে সংকটগুলোর সম্মিলিত একটি গুণ হলো, সংকট যে ধরণের হোক, তাতে প্রচুর পরিমাণ বেকারত্ব সৃষ্টি করে, জনসাধারণের রপ্তানি কমে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে লস শুরু হয়ে যায় এবং প্রচুর পরিমাণ সম্পদ বাজেয়াপ্ত হতে থাকে। সর্ববাস্থায় পুঁজিবাদের সংকটের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ জনসাধারণকেই বয়ে নিতে হয়। যাদের পুঁজিবাদি শেয়ার বা পুঁজিবাদি কর্মনীতির সাথে কোনোরকম সম্পর্ক নেই।
‘সংকট’ পুঁজিবাদি জ্ঞানত্ত্বের অযৌক্তিকতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। পুঁজিবাদি ব্যবস্থায় কোনো বস্তু বা কাজের মূল্য নির্ধারণ করা হয় মূলত একটি অনুমানের ভিত্তিতে—কাজটি হলে পুঁজি প্রবৃদ্ধি কতটা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এই ‘অনুমান’-এর জন্য কার্যকরী কোনো পদ্ধতি পুঁজিবাদে নেই, যার মাধ্যমে পুঁজির প্রবৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিতে বলা যায়। প্রতিটি কোম্পানীর মেনেজম্যান্ট সর্বদা এই প্রশ্নের মাঝেই থাকে যে, কোনো নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে পুঁজিতে কতটা প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে। এই জন্য সুদ ও শেয়ার মার্কেটে ‘মূল্য নির্ধারণে’ হাতেগোণা কিছু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে। পুঁজিবাদের পলিসিগুলো কখনোই জনসাধারণের সম্পদের প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাজানো হয় না। সঞ্চয় বা লাভের গড় হার (Average rate of Profit এবং Average rate of Accumulatoin) কখনোই এভাবে চলে না যে, মূল্যের স্থিতিশীলতা ঠিক করে অর্থ ও মানবীয় উপকরণের মাধ্যমে অর্জিত লাভ পূর্ণ সমানভাবে ব্যবহৃত হবে।
পুঁজিবাদি রাষ্ট্র চাই তা লিবারেল হোক বা সমাজতন্ত্র, এমন কোনো আইনিনীতি প্রণয়ন করে না, যার মাধ্যমে মূল্যের স্থিতিশীলতা ঠিক করে উৎপাদনের উপকরণগুলো এমনভাবে ব্যবহৃত হবে, যার মাধ্যমে ক্রমবর্ধবান মূলধন সম্ভাব্য সমানহারে সকলের কাছে পৌঁছতে পারে। কেননা পুঁজিবাদি রাষ্ট্রগুলো যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে তারা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠি স্বার্থ বা অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করতেই রাষ্ট্রের সকল পলিসিগুলো নির্ধারণ করে। সেগুলো কোনো অর্থেই জনসাধারণের পুঁজির প্রতিনিধি নয়। পুঁজিবাদে কোনো নিরপেক্ষতা নেই। পুঁজিবাদে একমাত্র নিরপেক্ষতা এটাই যে, সমাজের সকল মানুষ তাদের যোগ্যতানুযায়ী পুঁজিবাদের উন্নতিকরণে নিজের সকল সম্পদ বিনিয়োগ করার সুযোগ পাবে। যাকে সুযোগের সমতা (Equlity of Opporturnity) বলে। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই ধারণা দেওয়া হবে, তোমার গুরুত্ব ততটুকুই, যা তুমি পুঁজিবাদের প্রবৃদ্ধিকে আরো বৃদ্ধি করার জন্য করেছো। পুঁজিবাদি সমাজ নিজের তৈরি নিরপেক্ষতার সংজ্ঞানুযায়ী একটি জালেম সমাজব্যবস্থা। পুঁজিবাদি মূল্যবোধ অনুযায়ী পুঁজিবাদি সমাজের বড় একটি অংশ সর্বদা বঞ্চিত ও অত্যাচারিত থাকে দুই কারণে—
১. পুঁজিবাদের প্রবৃদ্ধির কাজে সে নিজের যোগ্যতানুযায়ী অংশগ্রহণ করার সুযোগই পায়নি।
২. তাকে কাজের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তা পুঁজিবাদের উন্নতি সাধনে, তার অংশগ্রহণ অনুপাতে নয়।
এজন্য পুঁজিবাদি সমাজের এক অংশের হাতে সম্পদের পাহাড় জমতে থাকে। যার কারণে উৎপাদনের সকল উপকরণ ও ক্ষমতা সমাজের অল্পকিছু শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় দিকে বেকারত্ব ও কর্মহীনতা উর্ধ্বগতিতে বাড়তে থাকে। বর্তমান ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহে চাকরীজীবি ও শ্রমজীবী মানুষের সামষ্টিক সংখ্যা নিতান্ত কম এবং তা নিন্মমুখী। সমাজের বড় অংশ যারা শুধু পুঁজিবাদের চক্করে (যেমন শেয়ার মার্কেট, সুদি লোন) উদভ্রান্তের মত ঘুরে ফিরছে। এবং এই সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। এদের মধ্যে যুবক শ্রেণি থেকে নিয়ে ছাত্র, বেকার আর পেনশনের টাকায় চলা কোটি কোটি মানুষ রয়েছে। উন্নত পুঁজিবাদি রাষ্ট্রগুলোতে সমাজের এই বিশাল বেকার শ্রেণীকে সরকারি ভাতা আর ঋণের মাধ্যমে উন্নত জীবনের সুযোগ করে দেয়। সাথে গণতান্ত্রিক কিছু আন্দোলন ও মানবধিকার কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রেখে এই বোধ তাদের মাঝে বসিয়ে দেওয়া হয় যে, বেকরত্ব সত্ত্বেও পুঁজিবাদি এই জীবনব্যবস্থা পরিচালনায় আমি একজন অংশীদার। এবং এই ব্যবস্থা থেকে উপকার ভোগ করার অধিকার আমি আদায় করতে সক্ষম। এই কর্মকৌশল অনুন্নত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেমন ভারত, পাকিস্তানেও বেশ কার্যকর হয়েছে। যার কারণে বেকার আর বঞ্চিত মানুষরা শাসনব্যবস্থাকে দূর করার কোনো প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় না। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সাধারণ মানুষ জনপ্রতিরোধ কিছু আন্দোলন, যেমন পারমানবিক বিরোধী আন্দোলন, ওকুপাই বা ওয়াল স্ট্রিট দখল আন্দোলন অথবা পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন (যেগুলো বাস্তবিক অর্থে খেল-তামাশা আর ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই না)—এগুলোতে যুক্ত থাকতে পেরে প্রশান্তি লাভ করে। আর অনুন্নত রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে এই ধরনের আন্দোলন কিছুদিন পর ঘরানা কেন্দ্রিক আন্দোলন হয়ে যায়, যাদের কার্যক্রম নির্দিষ্ট কিছু শহরাঞ্চলেই শুধু চলে। এগুলোর অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়— না জনগণের সমর্থন পায়, না পুঁজিবাদি প্রতিষ্ঠান সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়।
অপুঁজিবাদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমরা বিভিন্ন সময় বিদ্রোহ দেখতে পাই। তার কারণ হলো সেখানের শাসকরা জনগণগের ঐ সমস্ত বিষয়াদি ও হকসমূহ পূরণের সুযোগ দেয় না, যা পুঁজিবাদি রাষ্ট্রে তারা ভোগ করতে পারতো। ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপে এবং ২০১১-এর পরে আরব দুনিয়াতে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখতে পাই, সেগুলো মূলত পুঁজিবাদি বিপ্লব ছিলো। সে আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের মৌলিক দাবি ছিলো, উদারনৈতিক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ও পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করে জীবনের মান উন্নয়ণ করা। মধ্য এশিয়া আর আরব বিশ্বে সেই বিপ্লবগুলো থেকে বিপ্লবীরা যে ফল তুলতে চেয়েছিলো তার কিছুই তারা অর্জন করতে পারেনি। এবং আমরা দেখি পুরো আরব বা এশিয়ার কোথাও ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
পুঁজিবাদের ভিতর পরস্পর বৈপরীত্ব প্রচুর পরিমাণ। যার কারণে পুঁজিবাদ প্রতিটি যুগেই গুরুতর সংকটে পতিত হয়েছে। এবং বিভিন্ন বিপ্লবের মুখে পড়ে তা ধ্বংসপ্রায় হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। কিন্তু পুঁজিবাদি ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো, যে বিশ্বাসের উপর তা প্রতিষ্ঠিত—স্বাধীনতা, সাম্য ও উন্নতি—এগুলো মানুষের নিকট ব্যাপকভাবে যুক্তির বিচারে গ্রহণযোগ্য মনে হওয়া। পুঁজিবাদ খ্রিষ্ট সমাজে তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, যখন তা খ্রিষ্টধর্মের আকিদা-বিশ্বাস থেকে মানুষের সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছে।
পুঁজিবাদ মানুষকে লোভী, হিংসুক আর স্বার্থবাজ বানিয়ে ফেলে। যার কারণে নিজ স্বার্থের অনুকূলে পুঁজিবাদি যুক্তিগুলো মানুষ সহজেই গ্রহণ করে নেয়। আর এই লোভী, হিংসুক আর স্বার্থবাজী মানসিকতার কারণেই রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পুঁজিবাদি পলিসিগুলো অধিক যৌক্তিক মনে হয়। যতদিন মানুষ পশ্চিমা স্বাধীনতা, সাম্য আর উন্নতি—পুঁজিবাদি এই তিন নীতির উপর বিশ্বাস রাখবে এবং এগুলোর অর্জনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করবে, ততদিন পুঁজিবাদি ব্যবস্থা তার সকল সংকট কাটিয়ে উঠবে এবং সকল বাধা উপড়ে ফেলতে সক্ষম হবে। কারণ, পুঁজিবাদি জীবনব্যবস্থাই সেই স্বাধীনতা, সাম্য আর উন্নতি অর্জনের সকল সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। মোটকথা, পশ্চিমের তৈরি স্বাধীনতা, সাম্য আর উন্নতির উপর রাখা ব্যক্তিদের বিজয় বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদি জীবন ব্যবস্থার বিজয়েরই সমর্থক।
পুঁজিবাদ স্বভাবজাত বা বিজ্ঞানসম্মত কোনো ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি নয়, বরং পুঁজিবাদ একটি মানুষ্য স্বভাববিরুদ্ধ ও ভ্রান্ত জীবনব্যবস্থা, যা খোদার সাথে বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জীবন ব্যবস্থার পূর্ণ বিনাশ ছাড়া ইসলামের সংরক্ষণ ও বিজয় কখনোই সম্ভব নয়। তাই পুঁজিবাদি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলোৎপাটন করা বর্তমান সময়ের মুসলিমদের উপর ‘ফরজে কিফায়া’ দায়িত্ব। প্রত্যেক মুসলিম ও মুসলিম সংগঠনের জন্য নিজ নিজ অবস্থান থেকে পুঁজিবাদি জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা উচিত।
টিকাঃ
১.স্কলাসটিজম ইউরোপের দর্শন শাস্ত্রের বিকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম। ইউরোপে যখন দর্শনচর্চার প্রভাব বাড়তে থাকে, তখন খ্রিস্টানধর্মীয় বিষয়কে যুক্তির আলোকে প্রমাণ করার একটি প্রবণতা শুরু হয়। এই কাজে যেমন গির্জার পাদ্রিরা ছিলো তেমন সাধারণ খ্রিস্টধর্মের দিক্ষিতরাও অংশগ্রহণ করে। তাদের কাজ ছিলো প্রাচীন গ্রিসের, বিশেষ করে প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দার্শনিক মত দিয়ে খ্রিস্টধর্মের যুক্তিযুক্ত ভিত দাঁড় করানো। যারা এই কাজ করতো, তাদের স্কলাসটিক’ সম্প্রদায় বলা হতো। দেখুন, দর্শনকোষ-সরদার ফজলুল করিম, পৃষ্ঠা ৩২৭ (মাওলা ব্রাদার্স ২০২১) তাই স্কলাসটিজম কী তা সহজ ভাষায় বললে এতটুকু বলা যায়, ধর্মের আকিদা-বিশ্বাসকে ধর্মের উৎস থেকে প্রমাণ দেওয়ার বদলে যুক্তিশাস্ত্র দিয়ে প্রমাণ করা।
২.ব্যাংকো হলো ইটালির ফ্লোরেন্স শহরে শুরু হওয়া আধুনিক ব্যাংকের প্রথমরূপ।
৩.যদিও চুক্তি ছিলো সকল রাষ্ট্র আইএমএফের মাধ্যমে নিজেদের মুদ্রার মান ঠিক করবে, কিন্তু দেখা গেলো অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই আইন মানলো না। ১৯৪৬ সালে ব্রিটেন নিজেদের পাউণ্ডের মূল্য আইএমএফের অনুমতি ছাড়াই নিজেরাই ঠিক করে নেয়। (জাভেদ আকবর)
৪.অর্থনীতিতে মার্কেট কোনো নির্দিষ্ট জায়গা বা প্রতিষ্ঠানের নাম না, মার্কেট হলো এমন প্রতিটি সম্পর্ক যার ভিত্তিতে পন্য ও সেবার বিনিময়ে অর্থের লেনদেন হয়।